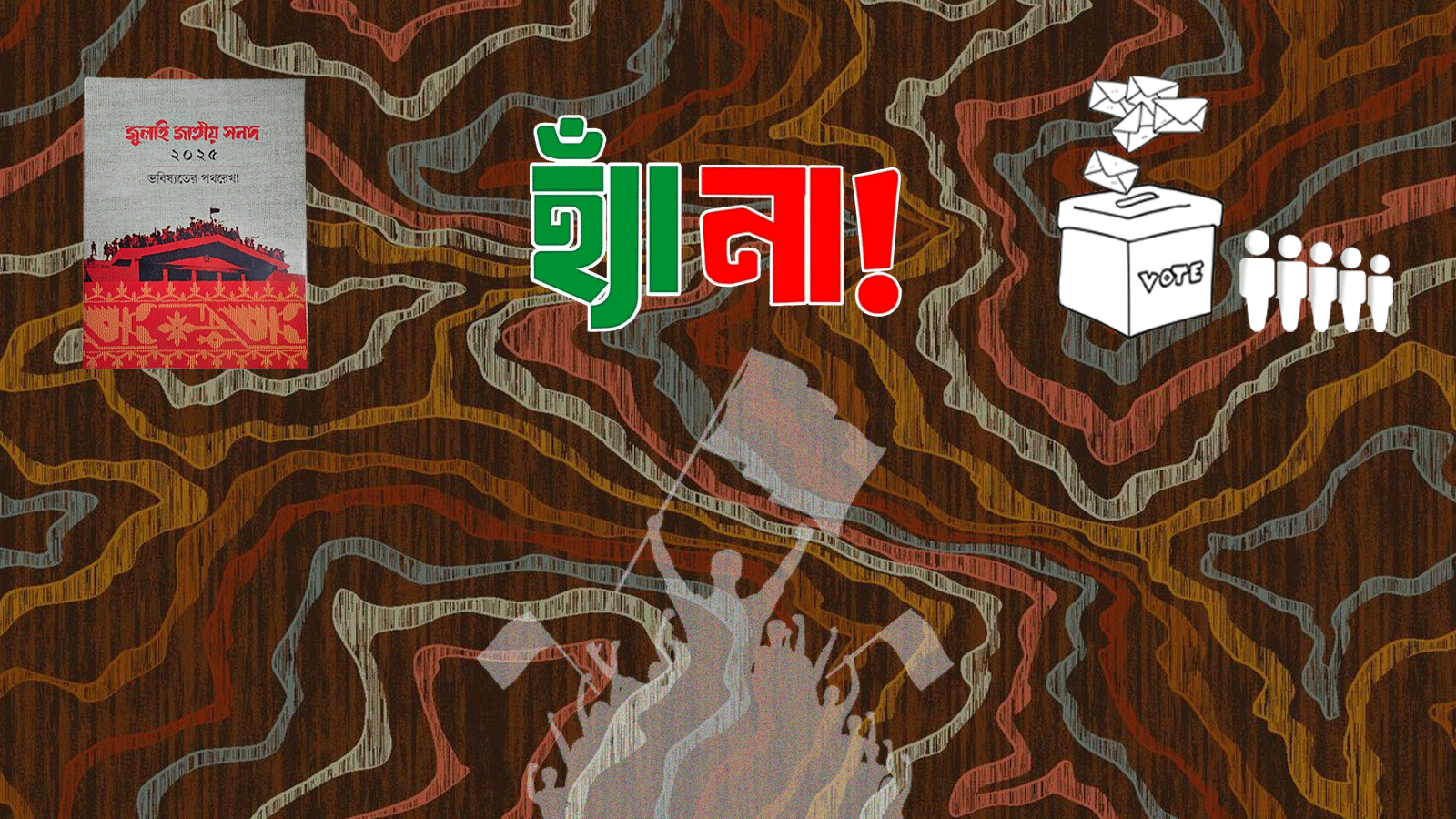আজ ১৪ ডিসেম্বর। এই দিনটি বাংলাদেশে প্রতিবছর রাষ্ট্রীয়ভাবে শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস হিসাবে পালিত হয়। এ দিনটি গভীর বেদনার, শোকের অশ্রু ঝরানো এবং স্বজন হারানোর কষ্টে কাতর। আজকের এই দিনে সাবিনা ইয়াসমিনের কণ্ঠ থেকে যখন শুনি-সব ক’টা জানালা খুলে দাও না/ওরা আসবে চুপি চুপি/যারা এই দেশটাকে ভালোবেসে দিয়ে গেছে প্রাণ-হৃদয়টা শিক্ত হয়ে ওঠে, অশ্রুধারা রোধ করা যায় না, হারানো স্বজনদের কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলা যায় না। এমন দিনেই তো বলা যায়-বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা, এর যত মূল্য সে কি ধরার ধুলায় হবে হারা। না, তাদের রক্তস্রোত শুকিয়ে যায়নি, মায়ের অশ্রুধারা ধরার ধুলায় হারিয়ে যায়নি। আজও সে রক্ত, সে অশ্রুধারা ফিনকি দিয়ে উৎক্ষিপ্ত হয়ে চলেছে। এর কোনো বিরতি নেই, বিরাম নেই।
’৭১-এর ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর অবধি এমন কোনো দিন নেই, রাত নেই, পল নেই, দণ্ড নেই-যে মুহূর্তে আমরা একজন স্বজনকে হারাইনি। এই স্বজন রক্তের সম্পর্কে স্বজন না হলেও জাতীয়তার পরিচয়ে পিতামাতা বা ভ্রাতা-ভগিনী হিসাবে অতি আপনজন। মুক্তিযুদ্ধের আগে আমরা প্রতিজ্ঞা করেছিলাম-দিয়েছি তো রক্ত, আরও দেব রক্ত, প্রয়োজন হলে দেব এক নদী রক্ত। রক্ত তো আমরা দিয়ে যাচ্ছি। রক্ত দিয়েছি অশোকের আমলে, রক্ত দিয়েছি সেনদের আমলে, রক্ত দিয়েছি মোগলদের আমলে, রক্ত দিয়েছি সিপাহি যুদ্ধে, জালিয়ানওয়ালা বাগে, সৈয়দ আহমদ বেরলভির জেহাদে, তিতুমীরের বাঁশের কেল্লায়, প্রীতিলতার আত্মাহুতির রক্তদানে, ব্রিটিশ শাসনের ঔপনিবেশিকতায়। এদেশের মানুষ হাসিমুখে ফাঁসির দড়িতে প্রাণ দিয়ে গেছে। রক্ত আমরা আরও দিয়েছি ভাষার জন্য, গণতন্ত্রের জন্য, শিক্ষার জন্য, এক সূর্যের নিচে মানুষ মানুষের ভাই এমন অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য। আমরা অকাতরে এভাবে রক্ত দিয়েছি পাকিস্তানের ভিন্ন এক ধরনের ঔপনিবেশিকতায়। তাতেও পাকিস্তানিদের খায়েশ মেটেনি। বর্গির হামলাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে ওরা হামলা চালায় ’৭১-এ। ’৭১-এর সেই দিনগুলোয় পাকিস্তানি সেনাদের নিষ্ঠুরতায় আমরা যাদের হারিয়েছি, তাদের হারানোকে বলি গণহত্যা। গণহত্যায় যারা শহিদ হয়েছিলেন, তারা ছিলেন আমজনতা।
বুদ্ধিজীবী হত্যার প্রকৃত খুনিদের আজও শনাক্ত করা হয়নি। শহিদ বুদ্ধিজীবীদের সন্তানরা আজও অনেকেই জীবিত আছেন। তারা শুধু এটুকু বলতে পারেন, বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে। কবে তারা স্বজন হারানোর জন্য বিচার পাবেন? বুদ্ধিজীবী হত্যার একটি ক্লু ১৯৭২-এর সংবাদপত্রে প্রকাশ পায়। তৎকালীন দৈনিক বাংলায় এ সংক্রান্ত প্রতিবেদনটি লিখেছিলেন প্রয়াত ড. ভুঁইয়া ইকবাল।
দেশের জন্য জীবন দেওয়া আমজনতা ও বুদ্ধিজীবীর মধ্যে ভেদরেখা আনা যুক্তিযুক্ত নয়। দেশের জন্য যারা প্রাণ দেন, তারা সবাই মহান শহিদ, মহান দেশপ্রেমিক। তাই তো কবি গেয়েছেন, ‘মুক্তির মন্দির সোপানতলে/কত প্রাণ হলো বলিদান/লেখা আছে অশ্রুজলে।’ যাদের নাম লেখা আছে অশ্রুতে, তাদের মধ্যে আমরা কীভাবে বিভাজন করি? আমজনতাই হোক আর বুদ্ধিজীবীই হোক, সবারই নাম লেখা আছে অশ্রুতে। আমরা কাউকে কোনোমতে ভুলতে পারি না। তারা সবাই আমাদের চলার পথে প্রেরণাদায়ী মহামানব। তবুও নিয়ম করা হয়েছে পৃথকভাবে ১৪ ডিসেম্বর শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালনের। এ দিবস বিশেষভাবে পালনের কারণও আছে। সেই পাকিস্তানি সময় থেকে বুদ্ধিজীবীদের একটি অংশকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা হয়েছিল। বলা হতো তারা পাকিস্তানের দুশমন। শিশুরাষ্ট্র পাকিস্তানকে অসময়ে পঙ্গু করে দেওয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তারা তাদের লেখনী দিয়ে জনগণের বিভিন্ন অংশের মধ্যে বিদ্বেষ ছড়ায়। তারা বাঙালিদের বলে, পাঞ্জাবিরা তাদের শত্রু। তারা বলে, বাঙালিরা পাঞ্জাবিদের ঘৃণার চোখে দেখে। এসব শিক্ষিত উচ্চ ডিগ্রিপ্রাপ্ত ব্যক্তি দেশের জন্য ঘোর বিপদ ডেকে আনবে। তাই তাদের চোখে চোখে রাখা হতো। তাদের সব ধরনের কাজে নজর রাখা হতো।
পাকিস্তান রাষ্ট্রটি ক্রমান্বয়ে গোয়েন্দাদের দখলে চলে যাচ্ছিল। অথচ এ পরিস্থিতি কারোরই কাম্য ছিল না। পাকিস্তানি শাসনক্ষমতায় বাঙালি নেতৃত্ব ক্রমান্বয়ে প্রান্তিকতায় পর্যবসিত হচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত একটি সুষ্ঠু সাধারণ নির্বাচনে তাদের বিজয় সহ্য করা হলো না। বন্দুকের বুলেটে তাদের বিজয় ছিনিয়ে নেওয়ার সর্বাত্মক আয়োজন করা হলো। পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য বাঙালি নেতাদের অবদান ছিল ঈর্ষণীয়। ১৯৪০ সালের লাহোরে পাকিস্তান প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন বাঙালিদের প্রিয় নেতা শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক। ১৯৪৬-এ বাঙালি মুসলমানরা ব্যাপকভাবে ভোট দেয় পাকিস্তান সৃষ্টির পক্ষে। পাকিস্তানের জন্য এত ত্যাগ স্বীকার করলেও পাকিস্তান রাষ্ট্রের কাঠামোয় পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের মর্যাদার আসন থেকে বঞ্চিত করা হয়। এ কারণে ক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছিল। বুদ্ধিজীবীরা তাদের লেখনীতে, বচনে, ভাষণে এই ক্ষোভকে অগ্নিস্পর্শী করে তুলেছিলেন। এ কারণে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের বিশেষভাবে শত্রুর তালিকাভুক্ত করা হয়। বেছে বেছে তাদের হত্যা করা হয়। অনেকের লাশ খুঁজে পাওয়া যায়নি। শুধু রাজধানী ঢাকাতেই নয়, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিক্ষক, অধ্যাপক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, পুলিশ অফিসার, শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, চলচ্চিত্রকার ইত্যাদি মাথা তোলা মানুষদের নিজ বাসভবন থেকে তুলে নিয়ে কাদামাখা বাসে করে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হয়।
বুদ্ধিজীবী হত্যার প্রকৃত খুনিদের আজও শনাক্ত করা হয়নি। শহিদ বুদ্ধিজীবীদের সন্তানরা আজও অনেকেই জীবিত আছেন। তারা শুধু এটুকু বলতে পারেন, বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে। কবে তারা স্বজন হারানোর জন্য বিচার পাবেন? বুদ্ধিজীবী হত্যার একটি ক্লু ১৯৭২-এর সংবাদপত্রে প্রকাশ পায়। তৎকালীন দৈনিক বাংলায় এ সংক্রান্ত প্রতিবেদনটি লিখেছিলেন প্রয়াত ড. ভুঁইয়া ইকবাল। ড. ভুঁইয়া ইকবাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এমএ পাশ করার পর কিছুদিন দৈনিক বাংলায় প্রতিবেদক হিসাবে কাজ করেন। ড. ভুঁইয়া ইকবাল আমার নেতৃত্বাধীন ছাত্রসংগঠনের সঙ্গে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তার সঙ্গে আমারও অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা ছিল। তার বাবা তৎকালীন গভর্নর হাউজে চাকরি করতেন। ভারতীয় বিমানবাহিনী গভর্নর হাউজে (বর্তমান বঙ্গভবন) স্ট্রেফিং করলে গভর্নর হাউজটি লন্ডভন্ড হয়ে যায়। দাপ্তরিক কাগজপত্র ও আসবাবপত্র ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এই গভর্নর হাউজেরই একটি কক্ষে অফিস করতেন গভর্নর এমএ মালিকের উপদেষ্টা মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী। ভারতীয় বিমানবাহিনীর স্ট্রেফিংয়ের ফলে রাও ফরমান আলীর সেক্রেটারিয়েট টেবিলটি কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যুদ্ধ শেষে ড. ভুঁইয়া ইকবাল (তখনও তিনি ড. হননি) রাও ফরমান আলীর অফিসকক্ষে তার ব্যবহার করা ডায়েরিটি খুঁজে পান। এ ডায়েরিতে কয়েকজন বাঙালি বুদ্ধিজীবী সম্পর্কে নেতিবাচক মন্তব্য লেখা ছিল। তাদের মধ্যে প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর নামও ছিল। ভুঁইয়া ইকবাল রাও ফরমান আলীর ডায়েরির বিষয়টি নিয়ে আমার সঙ্গে আলাপ করেন। আমি তাকে এ নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন দৈনিক বাংলায় প্রকাশের পরামর্শ দিই। আমি আরও বলি, প্রতিবেদনের সঙ্গে রাও ফরমান আলীর হাতে লেখার ফ্যাক্সিমিলিও ছাপিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করি। যথাযথভাবে প্রতিবেদনটি দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত হলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। বুদ্ধিজীবী হত্যায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সরাসরি যোগাযোগ থাকার বিষয়টি এখন আর লুকানো সম্ভব নয়।
পাকিস্তানিরা বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের কত তীব্রভাবে অপছন্দ করত, তা বোঝা যায় কিছু ঘটনাবলির মধ্য দিয়ে। শুধু বুদ্ধিজীবী নয়, বাংলা ভাষাভাষী জনগণকেও ঘৃণা করত পশ্চিম পাকিস্তানের সামন্তগোষ্ঠী। এক্ষেত্রে বাঙালিদের সম্পর্কে ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান তার আত্মজীবনী ‘ফ্রেন্ডস নট মাস্টার্স’ গ্রন্থে লিখেছেন, ‘পূর্ববঙ্গের মানুষ ছিল জনসংখার সবচেয়ে বড় অংশ। সম্ভবত তারা ছিল ভারতের প্রাচীনতম জনগোষ্ঠী।
পাকিস্তানের সামরিক কর্মকর্তারা ভীষণভাবে অপছন্দ করত বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের। তবে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের ক্ষুদ্র একটি অংশ পাকিস্তানিদের সঙ্গে কোলাবোরেট করেছিল। তারা চিন্তা ও মননের দিক থেকে ছিল ১৯৪৭-এর ১৪ আগস্টের বন্দিদশায়। ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন, ড. হাসান জামান ও ড. মোহর আলীর মতো ব্যক্তিরা চিন্তার রাজ্যে থমকে গিয়েছিলেন ১৯৪৭-এ। ১৯৪৭-পরবর্তী সময়ে আমাদের এ অঞ্চলের মানুষের ধীরে ধীরে মোহমুক্তি ঘটছিল। ১৯৪৭-এ পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় অনেক বুদ্ধিজীবী তাদের জ্ঞানসম্পদ ব্যবহার করেছিলেন। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭০-এই ২৩ বছর সময়ে এ অঞ্চলের সাধারণ মানুষের রাষ্ট্রচিন্তার ক্রমবিকাশ ঘটতে থাকে। এ ক্রমবিকাশের পথ ধরে তারা নিজেদের আবিষ্কার করেন নতুন এক রাষ্ট্রের যোদ্ধা হিসাবে।
পাকিস্তানিরা বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের কত তীব্রভাবে অপছন্দ করত, তা বোঝা যায় কিছু ঘটনাবলির মধ্য দিয়ে। শুধু বুদ্ধিজীবী নয়, বাংলা ভাষাভাষী জনগণকেও ঘৃণা করত পশ্চিম পাকিস্তানের সামন্তগোষ্ঠী। এক্ষেত্রে বাঙালিদের সম্পর্কে ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান তার আত্মজীবনী ‘ফ্রেন্ডস নট মাস্টার্স’ গ্রন্থে লিখেছেন, ‘পূর্ববঙ্গের মানুষ ছিল জনসংখার সবচেয়ে বড় অংশ। সম্ভবত তারা ছিল ভারতের প্রাচীনতম জনগোষ্ঠী। বলা বাহুল্য, তারা পাকিস্তান সৃষ্টির আগ পর্যন্ত স্বাধীনতা বা সর্বভৌমত্বের কোনো স্বাদ পায়নি। তারা কখনো শাসিত হয়েছে বর্ণ হিন্দুদের দ্বারা, কখনো মোগলদের দ্বারা, কখনো পাঠানদের দ্বারা, আবার কখনো ব্রিটিশদের দ্বারা। তারা অতীতের মতো এখনো হিন্দু সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত প্রভাবের অধীনে রয়ে গেছে। তাদের মধ্যে নিপীড়িত জাতিগোষ্ঠীর সব ধরনের মানসিক জড়তা লক্ষ্য করা যায়। ফলে সদ্য পাওয়া স্বাধীনতার সঙ্গে তারা সামাজিক ও মানসিকভাবে মানিয়ে নিতে পারেনি। আর এই ঐতিহাসিক পটভূমির কারণেই তাদের মধ্যে জটিলতা, বিচ্ছিন্নতাবোধ, সন্দেহপ্রবণতা এবং এক ধরনের আত্মরক্ষামূলক আক্রমণাত্মক মনোভাব দেখা যায়।’
এ তো গেল বাঙালিদের সম্পর্কে পাকিস্তানের এক সাবেক প্রেসিডেন্টের মন্তব্য। মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে ভারতের বিমানবাহিনী গভর্নর হাউজে (বর্তমান বঙ্গভবন) স্ট্র্যাফিং করার পর গভর্নর হাউজের বেশ ক্ষতি হয়। এ ভবনেই বসতেন পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তা মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী। তিনি ছিলেন অবরুদ্ধ পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নরের উপদেষ্টা। ১৬ ডিসেম্বরের পর রাও ফরমান আলীর রুমে একটি ডায়েরি পাওয়া যায়। ডায়েরিটি রাও ফরমান আলীর ব্যবহৃত টেবিলের ওপর পড়ে ছিল। ডায়েরিটি পেয়েছিলেন ভুইয়া ইকবাল। ভুইয়া ইকবাল পরবর্তী সময়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক ছিলেন। ওই সময় তিনি দৈনিক বাংলায় সাংবাদিক হিসাবে কাজ করতেন। ভুইয়া ইকবাল ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের সক্রিয় সদস্য। ডায়েরিটি তিনি আমাকে দেখিয়েছিলেন। ওই ডায়েরিতে প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীসহ কয়েকজন বুদ্ধিজীবীর ওপর লেখা নোট ছিল। আমি ভুইয়া ইকবালকে এই ডায়েরির ওপর একটি প্রতিবেদন লেখার পরামর্শ দিই। আমি তাকে বলেছিলাম, ইতিহাসের বিচারে এ প্রতিবেদনটি খুবই সময়োপযোগী ও মূল্যবান হবে। দৈনিক বাংলায় প্রতিবেদনটি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল।
বুদ্ধিজীবী হত্যা সম্পর্কে আমাদের সমাজে দুরকমের তত্ত্ব আছে। প্রথম তত্ত্বটি হলো, পাকিস্তানি সেনারা তাদের দালালদের দিয়ে বুদ্ধিজীবী হত্যার ঘটনাটি ঘটিয়েছিল। এ হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনী নতুন দেশ বাংলাদেশকে মেধাশূন্য করার চেষ্টা চালিয়েছিল। দ্বিতীয় তত্ত্বটি হলো, এটা ভারতীয় গোয়েন্দাদের কাজ। ভারত নাকি চেয়েছিল বাংলাদেশ মেধাশূন্য হয়ে গেলে ভারত থেকে আনা বুদ্ধিজীবী ও প্রশাসকদের দিয়ে নতুন রাষ্ট্রের অফিস-আদালত ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্ম চালানো হবে। যা হোক, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভারতীয় সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা জেনারেল বিএন সরকার সার্বিকভাবে বাংলাদেশের প্রশাসনকে সহায়তা করার ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। কিন্তু ভারতের এ ধরনের সহায়তার প্রস্তাব প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান অগ্রাহ্য করেন।
বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা হয়েছিল মোটামুটিভাবে দুই পর্বে। ২৫ মার্চের কালরাত্রিতে যখন পাকিস্তানি সেনারা অপারেশন সার্চলাইট শুরু করল, তখন সে রাতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কজন স্বনামধন্য শিক্ষককে হত্যা করা হয়েছিল। তাদের মধ্যে ছিলেন দার্শনিক গোবিন্দ্র চন্দ্র দেব, জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, মনিরুজ্জামান প্রমুখ।
দেখা যাচ্ছে, বুদ্ধিজীবী হত্যা সম্পর্কে আমরা খুব কমই জানি। এ বিভ্রম থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য জ্ঞানী-গুণী বোদ্ধা মানুষকে দিয়ে একটি কমিশন গঠন করতে হবে। এ কমিশনের দায়িত্ব হবে বুদ্ধিজীবী হত্যার নীলনকশা এবং এর বাস্তবায়ন সম্পর্কে সব ধরনের তথ্য আহরণ করে বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের ওপর আলোকপাত করা। এ কাজটি না করা হলে জাতি হিসাবে আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের ওপর অবিচার করব। এ অবিচার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতিও সমভাবে করা হবে।
বুদ্ধিজীবী হত্যার একটি প্রামাণ্যদলিল প্রকাশ করা অপরিহার্য। বাংলাদেশের ঊষালগ্নে দেশের সাংবাদিকরা বেশকিছু অনুসন্ধানী প্রতিবেদন লিখেছিলেন। এসব প্রতিবেদন দেশের গুরুত্বপূর্ণ দৈনিক ও সাপ্তাহিকগুলোয় প্রকাশিত হয়েছিল। এসব প্রতিবেদনে ২০-২৫ জন শহিদ বুদ্ধিজীবী কীভাবে নিজ বাসভবন থেকে ধৃত হলেন, কীভাবে একটি কাদামাখা বাসে তাদের চোখ বেঁধে তুলে নেওয়া হয়েছিল এবং বধ্যভূমিতে তাদের লাশ কীভাবে শনাক্ত হয়েছিল, সে সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। তবে কিছু বুদ্ধিজীবীর লাশ পাওয়া যায়নি। বুদ্ধিজীবীদের যখন হত্যা করা হয়, তখন তাদের ওপর যে অবর্ণনীয় অত্যাচার চালানো হয়েছিল তার আভাস পাওয়া গেছে লাশগুলোর সুরতহালে।
বুদ্ধিজীবী দিবস এলে দেশের দৈনিক সংবাদপত্রগুলোয় একঝাঁক বুদ্ধিজীবীর ছবি দিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কেবল তাদেরই কি হত্যা করা হয়েছে? আমার ধারণা, বাংলাদেশের জেলা-উপজেলায় অবস্থানরত অন্য অনেক বুদ্ধিজীবীকেও হত্যা করা হয়েছে। তারা মফস্বলের বুদ্ধিজীবী। তাদের কেউ কলেজ বা স্কুলের শিক্ষক, কেউ চিকিৎসক, কেউ প্রকৌশলী এবং কেউ লেখক কিংবা কবি। তাদের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা হওয়া উচিত। মুক্তিযোদ্ধার তালিকা নিয়ে যেভাবে ছেলেখেলা হয়েছে, এমনকি দুর্নীতিও হয়েছে, সে রকম কিছু শহিদ বুদ্ধিজীবীদের তালিকা করার ক্ষেত্রে যদি ঘটে, তাহলে তা হবে খুবই দুঃখজনক। আমি বুদ্ধিজীবী হিসাবে যেসব পেশাদারের কথা বলেছি, তারা অপরিচিত মানুষ নন। এখনো তারা যে যেখানে ছিলেন সেখানকার মানুষ তাদের কথা স্মরণ করতে পারে। তবে আরও কিছুদিন গেলে স্মরণকারী মানুষদের পাওয়া যাবে না। ফলে শহিদ বুদ্ধিজীবীদের বৃহত্তর তালিকাও ত্রুটিমুক্ত থাকবে না। সময় দ্রুত পার হয়ে যাচ্ছে। অনেক কিছুই তো করা দরকার। শুধু তালিকা করার জন্য তালিকা নয়। তালিকাটি সঠিক হলে একখণ্ড সঠিক ইতিহাসও পাওয়া যাবে। দেশে একাত্তরের শহিদদের তালিকা করার দাবি আছে। এটি বাস্তবায়ন করতে হলে খুব ভেবেচিন্তে এবং আন্তরিকভাবে এগোতে হবে। শহিদ বুদ্ধিজীবীদের তালিকা করার আগে পদ্ধতি সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। তালিকা করার পদ্ধতিতে যদি ভুল থেকে যায়, তাহলে তালিকাটিও নির্ভুল হবে না। দুর্ভাগ্যের বিষয়, কোনো কাজের উদ্যোগ নিলে আমরা অনেক আওয়াজ-আয়োজন করি, কিন্তু ফল কী হবে তা ভেবে দেখি না। এরকম হলে পুরো ব্যাপারটি হয়ে যাবে পর্বতের মূষিক প্রসবের মতো।
বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা হয়েছিল মোটামুটিভাবে দুই পর্বে। ২৫ মার্চের কালরাত্রিতে যখন পাকিস্তানি সেনারা অপারেশন সার্চলাইট শুরু করল, তখন সে রাতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কজন স্বনামধন্য শিক্ষককে হত্যা করা হয়েছিল। তাদের মধ্যে ছিলেন দার্শনিক গোবিন্দ্র চন্দ্র দেব, জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, মনিরুজ্জামান প্রমুখ। শোনা যায়, পাকিস্তানি সেনারা হত্যা করতে চেয়েছিল বাংলার অধ্যাপক মনিরুজ্জামানকে। কিন্তু ভুল বুঝে তারা হত্যা করে পরিসংখ্যানের অধ্যাপক মনিরুজ্জামানকে। অধ্যাপক মনিরুজ্জামান আমাদের পরিসংখ্যানের ক্লাস নিতেন। অর্থনীতির অধ্যাপক ড. আনিসুর রহমানও পাকিস্তানি সেনাদের টার্গেটে ছিলেন। তিনি বেঁচে যান তার ফ্ল্যাটের দরজায় তালা মেরে রাখার ফলে। পাকিস্তানি সেনারা মনে করেছিল তিনি বাসায় নেই। মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে যেসব বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করা হয় তাদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, অধ্যাপক ফয়জুল মহি, অনুদৈয়পায়ন ভট্টাচার্য, ডাক্তার মর্তুজা, সাংবাদিক সিরাজুদ্দীন হোসেন, ডাক্তার আলিম চৌধুরী, অধ্যাপক আনোয়ার পাশা প্রমুখ। মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে যাদের হত্যা করা হয়েছিল, তাদের খুনিরা আলবদর বাহিনীর সদস্য ছিল বলে মানুষের বিশ্বাস। ঢাকার বাইরে পাকিস্তানি সেনারা হত্যা করে কুমিল্লার কংগ্রেস নেতা ধীরেন দত্তসহ অনেককে।
আমি মনে করি, বুদ্ধিজীবী নিধনযজ্ঞে যারা প্রাণ হারিয়েছেন, তাদের আরও মর্যাদার সঙ্গে স্মরণ করা উচিত। আমরা যে উদাসীন ও দায়িত্বহীন, তার প্রমাণ মেলে বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধের দেওয়ালটি সারা বছর অবহেলায় থাকার পর কেবল ১৪ ডিসেম্বর এলে তার ধোয়ামোছার আয়োজনে।
লেখক: শিক্ষাবিদ ও অর্থনীতিবিদ