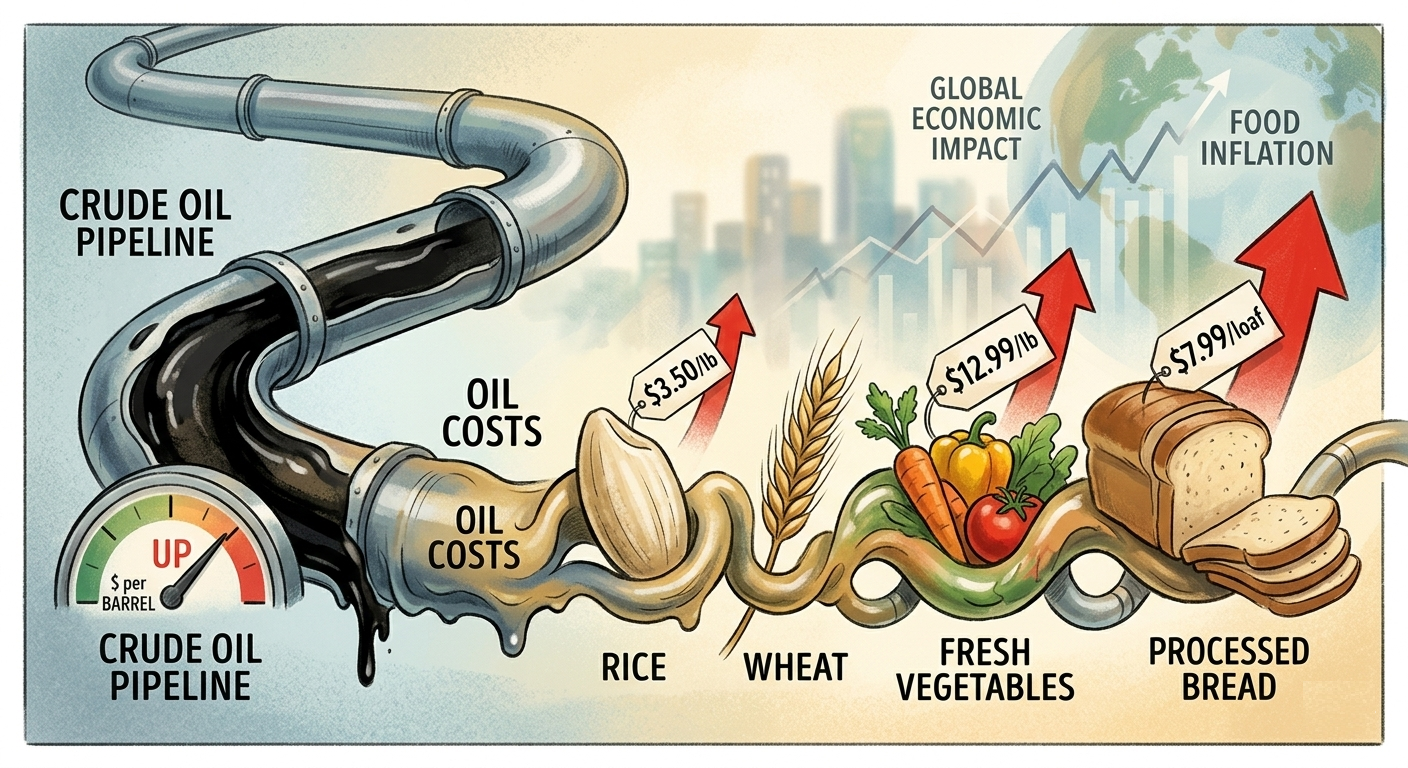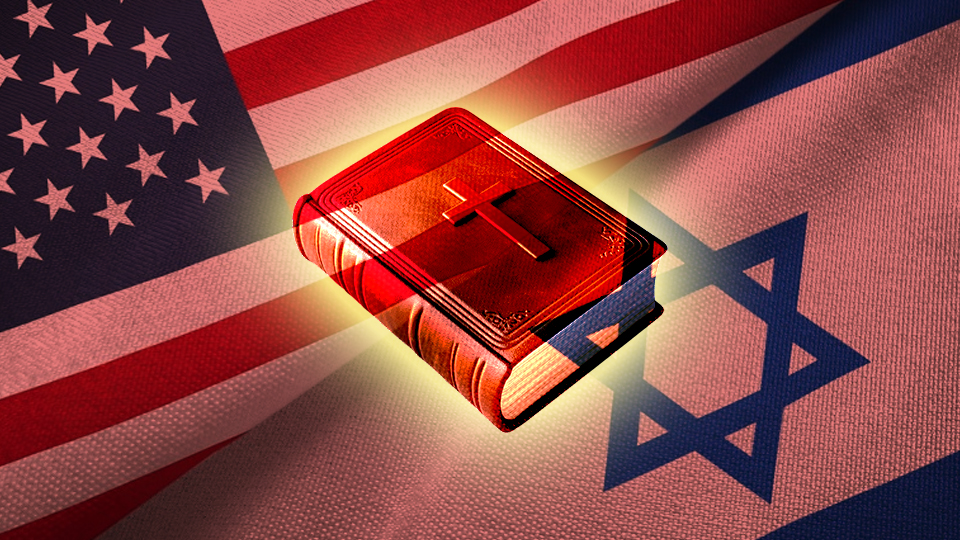মিয়ানমারে সামরিক অভ্যুত্থানের পর প্রায় পাঁচ বছর পেরিয়ে গেছে। এখন দেশটি নানাভাবে বিভক্ত। অভ্যুত্থানের পর শুরু হওয়া গৃহযুদ্ধে হাজারো মানুষ নিহত হয়েছে। প্রায় এক কোটি ৮০ লাখ মানুষ এখন মানবিক সহায়তার ওপর নির্ভরশীল। জান্তা সরকারের হাতে এখন দেশটির অর্ধেকেরও কম ভূখণ্ড নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। বাকি বিশাল এলাকাজুড়ে জাতিগত সশস্ত্র গোষ্ঠী ও বিদ্রোহী দলগুলো নিজেদের শাসন চালাচ্ছে।
এই ভাঙাচোরা রাজনৈতিক বাস্তবতা মিয়ানমারে দীর্ঘমেয়াদি অস্থিরতার ঝুঁকি তৈরি করেছে। এর প্রভাব দেশটির সীমান্ত পেরিয়ে অন্য দেশেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। তবে মিয়ানমারের সবচেয়ে প্রভাবশালী প্রতিবেশী চীন এই বিভাজনকে আর অস্থায়ী সমস্যা হিসেবে দেখছে না। বরং বেইজিং মনে করছে, এই অস্থিরতা দীর্ঘদিন ধরেই থাকবে।
গৃহযুদ্ধের বড় একটা সময় ধরে চীন সামরিক জান্তা ও সীমান্তবর্তী সশস্ত্র গোষ্ঠী—উভয়ের সঙ্গেই যোগাযোগ রেখেছিল। চীনের আশা ছিল, শেষ পর্যন্ত জান্তাই শক্তিশালী হয়ে দেশকে একত্রিত করবে। কিন্তু এখন চীনের কৌশল বদলেছে। তারা এখন জান্তা ও সীমান্তবর্তী সশস্ত্র গোষ্ঠী—উভয়ের ওপর সরাসরি প্রভাব ধরে রাখার কৌশল নিয়েছে।
চীন একদিকে জান্তাকে শর্তসাপেক্ষে অর্থনৈতিক ও মানবিক সহায়তা দিচ্ছে। অন্যদিকে সীমান্তের জাতিগত গোষ্ঠীগুলোর ওপর চাপ সৃষ্টি করছে। বিশাল অর্থনৈতিক প্রভাব কাজে লাগিয়ে চীন প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষগুলোকে নিজের শর্তে আলোচনায় বসতে বাধ্য করছে।
ফরেন অ্যাফেয়ার্সের বিশ্লেষণ মতে, এই প্রেক্ষাপটে ২৮ ডিসেম্বর শুরু হতে যাওয়া নির্বাচন মিয়ানমারে কোনো গণতান্ত্রিক রূপান্তর আনবে—এমন সম্ভাবনা কম। দেশীয় রাজনৈতিক দলগুলোর কিছু আশা থাকলেও আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকেরা এই নির্বাচনকে অবাধ ও সুষ্ঠু হবে বলে মনে করছেন না। তবু চীনের দৃষ্টিতে এই নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চীন ভাবছে, এই নির্বাচনের মাধ্যমে এমন একটি মিশ্র রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা যাবে, যেখানে সামরিক জান্তা প্রকৃত ক্ষমতা ধরে রাখবে, আর বেসামরিক সংসদ বাজেট ও চুক্তির মতো প্রশাসনিক কাজ করবে।
২০২১ সালের সামরিক অভ্যুত্থানের আগেই মিয়ানমারের বিভিন্ন এলাকায় জাতিগত সশস্ত্র গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণ ছিল। অভ্যুত্থানের পর শুরু হওয়া গৃহযুদ্ধ দেশটিকে আরও গভীরভাবে বিভক্ত করেছে। রাজধানী নেপিদোতে থাকা সামরিক জান্তা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ধরে রেখেছে এবং বড় শহরগুলো নিয়ন্ত্রণে আছে।
চীনের ধারণা, এতে তাদের জন্য বিনিয়োগ করা সহজ হবে। কারণ জান্তার আদেশ অনিশ্চিত হলেও বেসামরিকভাবে অনুমোদিত প্রক্রিয়া তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল ও আইনি নিরাপত্তা দেয়। ফলে দেশের যে অংশই যেভাবেই নিয়ন্ত্রিত হোক না কেন, চীনা কোম্পানিগুলো সুবিধা পাবে।
ফরেন অ্যাফেয়ার্স বলছে, এই নির্বাচন মিয়ানমারের বিভাজন দূর করবে না। বরং সেই বিভাজনকে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করবে, যাতে চীনের ঝুঁকি কমে। বেইজিং মনে করে, যতদিন প্রধান ক্ষমতাধর গোষ্ঠীগুলো বাণিজ্য, জ্বালানি ও প্রশাসনিক সমন্বয়ের জন্য চীনের ওপর নির্ভরশীল থাকবে ততদিন বিভক্ত মিয়ানমারে তাদের কোনো সমস্যা হবে না। তাদের বিশ্বাস, প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীগুলোর ওপর চাপ বাড়ানো বা কমানোর মতো যথেষ্ট সক্ষমতাও তাদের রয়েছে। এর মাধ্যমে এই ‘নিয়ন্ত্রিত বিশৃঙ্খলা’কে বড় ধরনের অস্থিরতায় রূপ নেওয়া থেকেও ঠেকানো সম্ভব।
বিচ্ছিন্ন জাতি: বিদ্রোহীদের জয় অনিশ্চিত
২০২১ সালের সামরিক অভ্যুত্থানের আগেই মিয়ানমারের বিভিন্ন এলাকায় জাতিগত সশস্ত্র গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণ ছিল। অভ্যুত্থানের পর শুরু হওয়া গৃহযুদ্ধ দেশটিকে আরও গভীরভাবে বিভক্ত করেছে। রাজধানী নেপিদোতে থাকা সামরিক জান্তা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ধরে রেখেছে এবং বড় শহরগুলো নিয়ন্ত্রণে আছে। তবে আরাকান আর্মি ও ইউনাইটেড ওয়া স্টেট আর্মির মতো শক্তিশালী জাতিগত গোষ্ঠীগুলো কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিস্তীর্ণ এলাকায় প্রশাসনিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে।
২০২৩ সালের শেষ দিকে ও ২০২৪ সালে সরকারবিরোধী বিদ্রোহী ও জাতিগত গোষ্ঠীগুলোর যৌথ অভিযান ‘অপারেশন ১০২৭’-এর সময় ৪০টির বেশি বড় শহর ও প্রশাসনিক কেন্দ্র জান্তার হাতছাড়া হয়। ২০২৫ সালের শুরুতে চীনের মধ্যস্থতায় হওয়া কিছু সমঝোতার পর সামরিক বাহিনী পাল্টা অভিযান শুরু করে এবং কিছু এলাকা পুনর্দখল করে। তবে উত্তর শান রাজ্যে হারানো ভূখণ্ডের মাত্র ১১ শতাংশই জান্তা পুনরুদ্ধার করতে পেরেছে। দেশের অনেক জায়গায় সামরিক সরকার কেবল প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ এলাকা ও গুরুত্বপূর্ণ পরিবহন পথের কাছে বিচ্ছিন্ন সামরিক ঘাঁটি ধরে রাখতে পেরেছে।
তবে জান্তার দুর্বলতা বিদ্রোহীদের নিশ্চিত বিজয়ের নিশ্চয়তা দেয় না। সরকারবিরোধী শক্তিগুলো নিজেদের মধ্যেই বিভক্ত। তাদের মধ্যে রয়েছে নির্বাসিত নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত ন্যাশনাল ইউনিটি গভর্নমেন্ট, পিপলস ডিফেন্স ফোর্স এবং স্বতন্ত্র জাতিগত সশস্ত্র সংগঠন। কিন্তু নেতৃত্ব ও কমান্ড কাঠামোর বিভাজন, অস্ত্রের ঘাটতি এবং প্রাকৃতিক সম্পদের আয় নিয়ে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের কারণে তারা একটি সমন্বিত কৌশল গড়ে তুলতে পারেনি। অপারেশন ১০২৭-এ সমন্বয়ের নজির দেখা গেলেও পরে তা ভেঙে পড়ে। ফলে চলমান অন্তর্দ্বন্দ্বই এখনো জান্তাকে উৎখাতের পথে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে আছে।
কিয়াউকফিউ বন্দর আনুষ্ঠানিকভাবে জান্তা সরকারের অধীনে হলেও বাস্তবে এর চারপাশের এলাকা ও পাইপলাইন পথ আরাকান আর্মির নিয়ন্ত্রণে। তবু চীন এই গোষ্ঠীর ওপর প্রভাব বজায় রেখেছে। কারণ বন্দরের প্রধান বিনিয়োগকারী ও ভবিষ্যৎ অর্থায়নের উৎস চীনই। এই প্রভাব কাজে লাগিয়ে চীন আরাকান আর্মিকে তার অবকাঠামো রক্ষায় বাধ্য করছে।
বিভাজনকে কাজে লাগিয়ে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা
মিয়ানমারের ভাঙা রাজনৈতিক বাস্তবতাকে চীন স্পষ্ট সুযোগ হিসেবে দেখছে। বেইজিং একই সঙ্গে সামরিক জান্তা ও শক্তিশালী জাতিগত সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। সব পক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার এই কৌশলের মাধ্যমে চীন তার অর্থনৈতিক ও কৌশলগত স্বার্থ নিশ্চিত করতে চায়। এর মধ্যে রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদের যোগান এবং স্থলপথে ভারত মহাসাগরে পৌঁছানোর পথ।
মিয়ানমার এখন চীনের ভারী বিরল খনিজ ধাতুর সবচেয়ে বড় সরবরাহকারী। এসব খনিজ বৈদ্যুতিক যান, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও আধুনিক প্রযুক্তিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ২০২৩ সালে চীন মিয়ানমার থেকে প্রায় ৪১ হাজার ৭০০ মেট্রিক টন ভারী বিরল খনিজ আমদানি করেছে, যা তার মোট চাহিদার ৯০ শতাংশের বেশি। তবে এই খনিজের বড় ভাণ্ডারগুলো কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে নয়। সেগুলো মূলত কাচিন ও শান রাজ্যে অবস্থিত, যেখানে জাতিগত সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর কার্যত নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। তাই এসব গোষ্ঠীর সঙ্গে কাজ না করলে চীনের সরবরাহব্যবস্থা টেকসই রাখা সম্ভব নয়।
এ ছাড়া চীন ভারত মহাসাগরে সরাসরি পৌঁছানোর পথও তৈরি করতে চায়। সে লক্ষ্যেই কুনমিং থেকে রাখাইন রাজ্যের কিয়াউকফিউ গভীর সমুদ্রবন্দর পর্যন্ত চীন-মিয়ানমার অর্থনৈতিক করিডর গড়ে তোলা হচ্ছে। বর্তমানে চীন মালাক্কা প্রণালির ওপর নির্ভরশীল, যা সামরিক সংকটে ঝুঁকিপূর্ণ। মিয়ানমারের মাধ্যমে সরাসরি সমুদ্রপথ পেলে চীনের জ্বালানি নিরাপত্তা ও কৌশলগত স্বাধীনতা বাড়বে।
কিয়াউকফিউ বন্দর আনুষ্ঠানিকভাবে জান্তা সরকারের অধীনে হলেও বাস্তবে এর চারপাশের এলাকা ও পাইপলাইন পথ আরাকান আর্মির নিয়ন্ত্রণে। তবু চীন এই গোষ্ঠীর ওপর প্রভাব বজায় রেখেছে। কারণ বন্দরের প্রধান বিনিয়োগকারী ও ভবিষ্যৎ অর্থায়নের উৎস চীনই। এই প্রভাব কাজে লাগিয়ে চীন আরাকান আর্মিকে তার অবকাঠামো রক্ষায় বাধ্য করছে।
মিয়ানমারে কাজ করতে গিয়ে চীন বুঝেছে, খণ্ডিত রাষ্ট্রে বিভিন্ন ক্ষমতাধর গোষ্ঠীর সঙ্গে লেনদেন এড়ানো যায় না। তবে শুধু সাময়িক সমঝোতা দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের জন্য যথেষ্ট নয়। এজন্য চীন জাতীয় পর্যায়ের অনুমোদন, মানসম্মত চুক্তি ও আইনি নিশ্চয়তা চায়। এই কাঠামো কেবল কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রই দিতে পারে, রাষ্ট্র যত দুর্বলই হোক না কেন।
এই বাস্তবতায় কেন্দ্রীয় সরকার ও জাতিগত গোষ্ঠীগুলোও একে অপরের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। কারণ উভয় পক্ষই শেষ পর্যন্ত চীনের ওপর নির্ভর করছে। কেন্দ্রীয় সরকার রাজস্বের জন্য প্রকল্পগুলো চায়। জাতিগত গোষ্ঠীগুলো চায় জাতীয় অনুমোদন ও বেইজিংয়ের স্বীকৃতি। চীন এই নির্ভরশীলতাকে কাজে লাগিয়ে প্রক্রিয়াগত শর্ত ও ভবিষ্যৎ বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে স্থিতিশীল সমঝোতা নিশ্চিত করছে।
ক্ষমতা যেহেতু মিয়ানমারে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে রয়েছে, তাই সব পক্ষকে এক ছাতার নিচে এনে জাতীয় শান্তিচুক্তি করা আপাতত বাস্তবসম্মত নয়। চীনের কৌশল হলো, দীর্ঘ ও জটিল শান্তি আলোচনায় না গিয়েই পারস্পরিক নির্ভরতা তৈরি করে ধীরে ধীরে নিজের লক্ষ্য আদায় করা।
মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার ভারসাম্যে প্রভাব ফেলতে চীন সরাসরি মধ্যস্থতা, অর্থনৈতিক চাপ এবং যৌথ নজরদারির কৌশল ব্যবহার করছে। বিশ্বের অন্য কোনো দেশে তারা এতটা সক্রিয় ভূমিকা নেয়নি। তবে এই প্রভাব ভৌগোলিকভাবে সীমিত।
ক্ষমতার নেপথ্য নিয়ন্ত্রকরা
মিয়ানমারে এখন মূল প্রশ্ন ‘জাতীয় ঐক্য’ ফিরিয়ে আনা নয়। ফলে, এখন প্রশ্ন হলো—চীন কি স্থায়ী বিভাজনের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা একটি শাসনব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে পারবে? নির্বাচনের পর চীনের ধারণা অনুযায়ী, বর্তমান শাসক মিন অং হ্লাইং অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট হিসেবে থাকবেন। একই সঙ্গে দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হবে কয়েকজন জ্যেষ্ঠ সামরিক কর্মকর্তার মধ্যে। এতে কোনো একক উত্তরাধিকারী উঠে আসার সুযোগ কমবে। চীনের লক্ষ্য হলো, নেপিদোর ভেতরে বিকল্প ক্ষমতাকেন্দ্র গড়ে ওঠা ঠেকানো।
মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার ভারসাম্যে প্রভাব ফেলতে চীন সরাসরি মধ্যস্থতা, অর্থনৈতিক চাপ এবং যৌথ নজরদারির কৌশল ব্যবহার করছে। বিশ্বের অন্য কোনো দেশে তারা এতটা সক্রিয় ভূমিকা নেয়নি। তবে এই প্রভাব ভৌগোলিকভাবে সীমিত। চীনের মূল মনোযোগ উত্তর ও পশ্চিম সীমান্ত এলাকায়। এখানেই রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ এবং ভারত মহাসাগরে পৌঁছানোর কৌশলগত পথ। ইউনানভিত্তিক চীনা নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সক্ষমতাও মূলত এসব সীমান্ত এলাকায় সীমাবদ্ধ। তারা দেশের কেন্দ্রীয় সমভূমি কিংবা পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলে একই মাত্রার প্রভাব রাখতে পারে না।
এই সীমাবদ্ধতার কারণে অন্য আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক শক্তির জন্য জায়গা তৈরি হয়েছে। ভারত ও থাইল্যান্ড মিয়ানমারের পশ্চিম ও দক্ষিণে সক্রিয় ভূমিকা রাখছে। তারা সীমান্ত নিরাপত্তা, বাণিজ্য এবং শরণার্থীদের জন্য মানবিক করিডর পরিচালনায় জড়িত। আসিয়ানভুক্ত দেশগুলো নীরব কূটনৈতিক সংলাপের মাধ্যমে জান্তা ও বিরোধী শক্তির মধ্যে যোগাযোগ বাড়াতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা চীনের প্রধান প্রভাবক্ষেত্রের বাইরে প্রশাসনিক সক্ষমতা গড়ে তোলা, জরুরি চিকিৎসা ও খাদ্য সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার সুযোগ রাখে।
একটি একক কেন্দ্রীয় শক্তিকে টিকিয়ে রাখার বদলে চীন স্থানীয় পর্যায়ের নানা সমঝোতার জোড়াতালি দিয়ে পরিস্থিতি সামাল দিতে চাইছে। এতে সাফল্যের সম্ভাবনা থাকলেও ঝুঁকিও বড়। সীমান্তে বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোকে শক্তিশালী করতে করতে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব দুর্বল হয়ে পড়তে পারে। সেই দুর্বলতা যদি অতিরিক্ত বেড়ে যায়, তবে রাষ্ট্র ভেঙে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হবে। এতে সীমান্ত অপরাধ, শরণার্থী স্রোত এবং জাতিগত সহিংসতা আরও ভয়াবহ রূপ নিতে পারে।
শেষ পর্যন্ত চীন এই বাজি ধরেছে যে, চলমান অস্থিরতার মধ্যেও সূক্ষ্ম ভারসাম্য বজায় রেখে তারা মিয়ানমারে নিজেদের স্বার্থ আদায় করতে পারবে।